ভাব সম্প্রসারণ HSC 2025
very important
১)ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ
২)সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা
৩)পথ পথিকের সৃষ্টি করে না
পথিকই পথের সৃষ্টি করে
৪)দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য
৫) প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তারই
৬) 'তুমি অধম- তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
৭) মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে
৮) প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়
চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ
৯) প্রাণ থাকলে প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না
১০) সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
১১)স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
১২)কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।
১৩) সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ
১৪) রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।
১৫) গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি
১৬)মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।
১৭) মিথ্যা শুনিনি ভাই
এ হৃদয়ের চেয়ে বর কোন মন্দির কাবা নাই
১৮)অতৃপ্তিই অসুখের মূল।
১৯)বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে
২০) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মাধ্যে, বয়সের মধ্যে ন।
ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ
এই প্রবাদবাক্যে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মানবিক গুণের উৎস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ শুধু শারীরিক চাহিদা পূরণ করে মহান হতে পারে না। ভোগ মানুষকে কেবল ব্যক্তিস্বার্থে আবদ্ধ করে রাখে, আর ত্যাগ শেখায় পরার্থে বাঁচতে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে আত্মসংযম, ত্যাগ ও দায়িত্ববোধের ভিতর দিয়ে।
একজন পিতা যখন নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়েন কিংবা একজন বিপ্লবী দেশের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন—তাদের ত্যাগ মানবতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। ত্যাগের মধ্যে থাকে আত্মজয়, থাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নিঃশব্দ দীপ্তি। ত্যাগ মানুষকে করে অসাধারণ, আলোকিত করে তার অন্তর।
অন্যদিকে, ভোগ মানুষের আত্মাকে করে ক্লান্ত, অস্তিত্বকে করে সংকীর্ণ। তাই কেবল ভোগে জীবন নয়, ত্যাগেই জীবনের সৌন্দর্য। এই ত্যাগ থেকেই প্রস্ফুটিত হয় মানবতার দীপ্ত রূপ। পরিশেষে বলা যায়, ত্যাগহীন জীবন কখনোই মহৎ হতে পারে না; ত্যাগের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে।
সংসারসাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা
এই কথাটি জীবনের গভীর সত্য তুলে ধরে। সংসার যেন এক উত্তাল সাগর—দুঃখ, কষ্ট, সংকট ও ব্যর্থতার ধারাবাহিক তরঙ্গ সেখানে অবিরাম আছড়ে পড়ে। প্রতিটি মানুষ এই সাগরে নিজের জীবনভেলা নিয়ে চলেছে। একমাত্র আশাই তাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচায়।
মানুষ যখন হারিয়ে ফেলে আপনজন, যখন দারিদ্র্য ঘিরে ধরে, কিংবা আশাভঙ্গ তাকে ক্লান্ত করে—তখনো সে বাঁচে, কারণ কোথাও না কোথাও সে আশার আলো দেখতে পায়। মা বাঁচেন সন্তানের ভবিষ্যতের আশায়, কৃষক লাঙল চালান ফসলের স্বপ্নে, রোগী অপেক্ষা করেন সুস্থতার আশায়। আশা মানুষকে সহনশীল করে তোলে, জোগায় সাহস ও সংগ্রামের প্রেরণা।
আশাহীন জীবন যেমন মৃতপ্রায়, তেমনি আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আশাই মনকে শক্ত করে, চোখে আনে নতুন দিগন্তের ছবি। তাই সংসারসাগরের দুঃখতরঙ্গে ডুবে না গিয়ে মানুষ আশার ভেলাতেই এগিয়ে চলে আলোর পথে।
এই প্রবাদ আমাদের শেখায়—আশা কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ আশা থাকলেই জীবন বাঁচে।
পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে
প্রবচনটি আত্মনির্ভরতা ও নেতৃত্বগুণের প্রতীক। পৃথিবীর প্রতিটি অগ্রগতি সেইসব মানুষদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, যারা সাহস করে অজানার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। পথ প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় না, বরং যারা লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে চলে, তারাই নতুন পথ গড়ে তোলে।
যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যজগতে নতুন পথ রচনা করেছিলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা আপসহীন মনোবলে গড়েছেন সাম্যের পথ। তারা অপেক্ষা করেননি কোনো পথের, বরং নিজের পায়ে তৈরি করেছেন চলার দিশা। পথিক যদি হতো কেবল আগের পথে হাঁটা, তবে পৃথিবী কখনোই সভ্যতা ও উন্নতির মুখ দেখত না।
এই প্রবচন আমাদের শেখায়—চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাই সাহসিকতার পরিচয়। নেতৃত্বের আসল মানে, নিজের কাজ ও আদর্শে অন্যদের পথ দেখানো। যারা ইতিহাস তৈরি করে, তারা নিজেরাই নিজের গন্তব্য ঠিক করে, নিজেরাই পথ খুঁজে পায়।
সুতরাং, ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব অপেক্ষা করে থাকা নয়, সাহস করে এগিয়ে যাওয়া। পথ না থাকলেও এগিয়ে যাও, কারণ পথ পথিককেই খোঁজে।
দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য
প্রবচনটি নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রবোধের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গঠিত। কেবল জ্ঞান থাকলেই মানুষ শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না। যদি সেই জ্ঞান দুর্জনের হাতে পড়ে, তবে তা আশীর্বাদ নয়, বরং অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জ্ঞান তখন হয়ে ওঠে ধ্বংসের হাতিয়ার।
ধরুন একজন ডাক্তার যদি সৎ না হন, তবে তার জ্ঞান মানুষের জীবন বাঁচানোর পরিবর্তে নষ্ট করতে পারে। একইভাবে, একজন দুর্জন রাজনীতিবিদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেন জ্ঞান ব্যবহার করে। তাই চরিত্রহীন জ্ঞানী মানুষ সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর।
শাস্ত্রেও বলা হয়েছে—‘শিক্ষিত শয়তান নিরক্ষর নির্বোধের চেয়ে ভয়ানক।’ বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিবোধ, সহানুভূতি ও মানবতাবোধ তৈরি করা।
এই প্রবচন আমাদের সতর্ক করে—জ্ঞানীর পোশাকে ছদ্মবেশী দুর্জনদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। যদি কেউ মেধাবী হয় কিন্তু তার চিন্তা নীচ, চরিত্র কলুষিত, তবে তাকে সম্মান নয়, বরং পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।
প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তারই
এই প্রবচনটি আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। জীবনে কেবল নিজের জন্য বেঁচে থাকলে সেটি নয় প্রকৃত জীবন। যারা সমাজ, দেশ বা আদর্শের প্রয়োজনে জীবন দান করতে প্রস্তুত, তারাই প্রকৃতভাবে বেঁচে থাকে—মানুষের হৃদয়ে ও ইতিহাসে।
শহীদদের কথা ভাবলে আমরা বুঝতে পারি, মৃত্যুর ভয় জয় করেই তারা জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। তাঁরা প্রয়োজনে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দেননি। একদিকে তারা হয়তো শারীরিকভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাদের কর্ম ও ত্যাগ অমর হয়ে আছে।
এই প্রবাদ আমাদের শেখায়—জীবনের গৌরব আসে কেবল তখনই, যখন তা আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়। যে কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ভাবে, সে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলেও বাঁচে না প্রকৃতভাবে।
জীবন তখনই মূল্যবান, যখন তা অন্যের উপকারে আসে। তাই সাহস ও আত্মোৎসর্গই বেঁচে থাকার আসল অধিকার নিশ্চিত করে।
তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
এই অসাধারণ পঙ্ক্তিটি উঠে এসেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম থেকে। এর অন্তর্নিহিত ভাব অত্যন্ত মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা-সমৃদ্ধ। মানুষ যখন দেখে চারপাশে অন্যায়, দুর্নীতি, হিংসা ও স্বার্থপরতা বেড়ে চলেছে, তখন অনেকেই সেই প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃত উত্তম ব্যক্তি সেই, যে অধর্মের মাঝে থেকেও নিজের ধর্ম রক্ষা করে, অন্ধকারে থেকেও আলোকে আঁকড়ে ধরে।
“তুমি অধম”—অর্থাৎ তুমি পাপাচারী, অসৎ, পরার্থহীন; কিন্তু তাই বলে আমি কেন নীতিহীন হব? উত্তম হওয়া তো এক ব্যক্তিগত দায়িত্ব, যা অন্যের ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। একজন প্রকৃত মানবিক ব্যক্তি কখনোই অন্যের পাপ দেখে নিজের চরিত্র বিসর্জন দেন না। বরং সেই পাপের প্রতিবাদ করে, নিজের আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠেন। যেমন, মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন অহিংসার মাধ্যমে—অধমকে দেখে নিজেও অধম হননি।
এটি আমাদের শেখায়—নৈতিকতা কখনো আপোষযোগ্য নয়। সমাজে পাপ বাড়লে আমাদের সৎ হওয়া আরও জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যায় দেখে প্রতিহিংসা নয়, বরং আরও মমতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়ের পথে চলাই হলো প্রকৃত উত্তমের পরিচয়।
এই ভাবটি আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। আমরা যদি প্রতিকূলতার মাঝেও নৈতিকতা রক্ষা করি, তাহলেই প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারি।
মনেরে আজ কহ যে, ভালো-মন্দ যাহাই আসুক, সত্যরে লও সহজে
এই ভাবনাটি আমাদের আত্মিক প্রশান্তি ও আত্মজয়ের পথ দেখায়। জীবনের পথে যেমন সাফল্য আসে, তেমনি আসে ব্যর্থতা, যেমন আনন্দ, তেমনি দুঃখ। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যকে গ্রহণ করতে জানে, সে কখনো জীবনচ্যুতি ঘটায় না।
এই কবি-উক্তি শেখায়, জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে সহজভাবে গ্রহণ করো। ভালো বা মন্দ, যা-ই আসুক, তা জীবনপথের একেকটি ধাপ। এই মনের শক্তি ও স্থিতধী অবস্থাই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ করে।
সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই বলেই আমরা কখনো কখনো নিজেকে প্রতারণার জালে জড়াই। আবার সুখ এলে আমরা ভুলে যাই দুঃখের দিনগুলো, আর দুঃখ এলে সুখের আশা বিসর্জন দিই। অথচ জীবন তো চলমান, প্রতিদিন এক নতুন অধ্যায়।
যিনি সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেন, তিনি ব্যর্থতায়ও অবিচল থাকেন, সফলতাতেও বিনয়ী থাকেন। এই শিক্ষাই দিয়েছে মহামানবেরা—বুদ্ধ, খ্রিস্ট, রবীন্দ্রনাথ—যাঁরা সত্যের পথে অনড় থেকেছেন।
সত্য গ্রহণ করার মানে জীবনের সব উত্থান-পতনের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা। এই ভারসাম্যই জীবনকে করে সুস্থ, মসৃণ, শান্তিময়।
প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক
এই প্রবাদটি আধুনিক পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটালেও তার বিনিময়ে প্রকৃতিকে করেছে ক্ষতবিক্ষত। বন উজাড়, নদী দূষণ, জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তি—সবই আধিপত্যবোধের ফল। কিন্তু প্রকৃতির উপর শাসন করে মানুষ কখনোই টিকতে পারবে না। বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানেই নিহিত আছে টিকে থাকার পথ।
মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান। সে তার রসদ, সৌন্দর্য, প্রাণ—সবই প্রকৃতি থেকে পায়। অথচ সেই মায়ের সঙ্গেই মানুষ আচরণ করছে নিষ্ঠুরভাবে। পরিবেশদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—এখন প্রয়োজন সখ্য, শাসন নয়।
মৈত্রীর অর্থ হলো—প্রকৃতির নিয়মকে সম্মান করা, তার ভারসাম্য রক্ষা করা, তাকে ভালোবাসা দেওয়া। বৃক্ষরোপণ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, টেকসই কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা—এসবই প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার উপায়।
এই প্রবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—মানুষ প্রকৃতির উপর নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেই উন্নতি করতে পারে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে প্রথমে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখতে হবে।
প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না
মানুষের শরীরে যেমন প্রাণ আছে, তেমনই প্রাণ আছে পশু-পাখির, কীট-পতঙ্গের মধ্যেও। কিন্তু যা মানুষকে ‘মানুষ’ করে তোলে, তা তার ‘মন’। এই মনই ধারণ করে বিবেক, মানবতা, প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, করুণা, আত্মসংযম। তাই কেবল বেঁচে থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না, মনুষ্যত্ব না থাকলে সে মানুষ নামধারী প্রাণী মাত্র।
এই প্রবাদটির গভীর তাৎপর্য আছে। একজন মানুষ যদি অসৎ হয়, নিষ্ঠুর হয়, মিথ্যাচারী হয়—তবে তার মধ্যে কেবল প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব নেই। সে কেবল নিজের স্বার্থে বাঁচে, সমাজ বা অন্যের উপকারে নয়। আবার একজন নিরক্ষর কৃষকও হতে পারেন সত্যিকার অর্থে মানুষ—যদি তার মধ্যে থাকে সততা, ভালোবাসা ও সহানুভূতি।
মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় তার কর্মে। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, পশুর প্রতি সহানুভূতি, দুঃস্থের পাশে দাঁড়ানো—এই সবই মানুষের মনকে মহৎ করে তোলে। মনহীন জীবনের মানে দেহের অস্তিত্ব, আত্মার নয়।
সুতরাং, শুধু প্রাণ ধারণ নয়—মনুষ্যত্বের চর্চাই জীবনের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, মনই মানুষকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সত্তা বানায়।
সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
এই প্রবচনটি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গভীরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সুশিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তকের তথ্য জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা এমন এক মানসিক ও নৈতিক বিকাশ, যা মানুষকে নিজের চিন্তায় সচেতন ও দায়িত্ববান করে তোলে। একজন সত্যিকার সুশিক্ষিত ব্যক্তি আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মানুশীলনের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানচর্চা চালিয়ে যান।
স্কুল-কলেজের শিক্ষাই যথেষ্ট নয়—সেই শিক্ষা তখনই সার্থক হয়, যখন ব্যক্তি নিজেকে বুঝে, নিজের ভুল শোধরায়, নতুন কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। স্বশিক্ষিত মানে, সে নিজের মনকে প্রশ্ন করে, নিজের চিন্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।
যেমন—স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর বা হুমায়ুন আজাদ—তাঁরা ছিলেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ভাবনাশীল ও স্বশিক্ষিত মানুষ। তাঁদের শিক্ষা ছিল জীবনকে বোঝার জন্য, সমাজকে বদলানোর জন্য।
এই প্রবাদ আমাদের অনুপ্রাণিত করে—আমরা যেন কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না থাকি, বরং নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে শিখি, যুক্তি দিয়ে বুঝি, এবং নৈতিকতায় নিজেকে গড়ি।
সুশিক্ষা তখনই সার্থক হয়, যখন তা মানুষকে করে আত্মানুসন্ধানী ও চিন্তনশীল। তাই বলা যায়—সুশিক্ষিত হতে হলে প্রথমেই হতে হয় স্বশিক্ষিত।
স্বদেশের উপকারে নাই যার মন, কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
এই প্রবচনটি আমাদের জাতীয়তাবোধ, মানবিকতা এবং সমাজপ্রীতির অন্তর্নিহিত তাগিদকে প্রকাশ করে। মানুষ কেবল নিজের স্বার্থের জন্য বাঁচে না, বরং তার একটি দায়বদ্ধতা থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি। যে ব্যক্তি এই দায় অস্বীকার করে, শুধু নিজের সুখ-সুবিধা নিয়ে ভাবে, সে প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়—সে আত্মকেন্দ্রিক এক আত্মা, যার মধ্যে মনুষ্যত্বের আলো নেই।
স্বদেশ মানে শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, তা একটি সংস্কৃতি, ইতিহাস, আত্মপরিচয়। নিজের দেশের উন্নয়নে, কল্যাণে, বিপদে-আপদে পাশে না দাঁড়ানো মানেই নিজের শিকড়কে অস্বীকার করা। এমন ব্যক্তিকে মানুষ বলা চলে না। কেননা পশু নিজের জন্যই বাঁচে, মানুষের বাঁচার মধ্যে থাকতে হয় দেশ ও সমাজের উপকার।
যাঁরা ইতিহাসে মানুষ হয়ে উঠেছেন, তাঁরা স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। শহীদ তিতুমীর, সূর্যসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—তাঁদের মধ্যে ছিল দেশপ্রেমের মহৎ আত্মা। তারা কেবল দেশকে ভালোবেসেছেন না, দেশের মানুষকেও ভালোবেসেছেন।
এই প্রবচন আমাদের শেখায়, নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতির কল্যাণে কাজ করাই প্রকৃত মানুষ হওয়ার চিহ্ন। নইলে আমরা মানুষের চেহারায় পশু হয়েই থেকে যাব।
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙা।
এই প্রবাদটির অন্তর্নিহিত ভাব হলো—মানুষের প্রকৃত মূল্য তার অন্তর ও চরিত্রে, বাহ্যিক রূপ-রঙে নয়। আমরা সমাজে প্রায়ই মানুষকে গায়ের রঙ, আর্থিক অবস্থা, পোশাক বা পদমর্যাদা দিয়ে বিচার করি। কিন্তু এসবের বাইরেই থাকে একজন মানুষের সত্য পরিচয়—তার মন, হৃদয়, চিন্তা, ও কর্ম।
মানুষের রং যেমনই হোক, তার ভিতরের রক্ত একরকম। কেউ কালো, কেউ ধলো—এই বিভাজন কেবল দৃষ্টিভ্রম। প্রকৃতি কাউকে নিচু বা উচ্চ করে সৃষ্টি করেনি; সমাজ ও সংস্কারই মানুষে মানুষে এই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করেছে।
এই ভাবটি আমাদের সাম্যের শিক্ষা দেয়। একজন কালো চামড়ার কৃষক যেমন মানবিক হতে পারেন, তেমনি এক ধনী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিও হতে পারেন নিষ্ঠুর ও নির্মম। ফলে রঙ নয়, মানুষ বিচার করতে হয় তার চরিত্র দিয়ে।
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বুদ্ধ, গান্ধী—এঁরা সব সময় এই সাম্যের কথা বলেছেন। নজরুল তো স্পষ্ট লিখেছেন—“গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান”।
এই প্রবাদ আমাদের কুসংস্কার ও বৈষম্য থেকে মুক্ত হতে শেখায়। এতে রয়েছে এক মানবিক সমাজ গঠনের দর্শন—যেখানে মানুষকে বিচার করা হবে মনুষ্যত্ব দিয়ে, রং দিয়ে নয়।
সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ
সাহিত্য একটি জাতির মনের আয়না। একটি জাতির চিন্তাধারা, জীবনদৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও স্বপ্ন সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়। এই প্রবাদটি ঠিক এই সত্যকেই তুলে ধরে। যেমন আয়নায় মুখ দেখা যায়, তেমনি সাহিত্যে জাতির আত্মপ্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।
যে জাতির সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, সেই জাতি ততটা উন্নত ও সচেতন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটি সমাজ তার মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে। একে বলা যায় জাতির আত্মার ভাষ্য।
বাংলা সাহিত্যও আমাদের জাতিসত্তা গঠনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের মানববাদ, নজরুলের বিদ্রোহ, জসীম উদ্দীনের গ্রামীণ জীবনচিত্র—সবই আমাদের জাতিকে পরিচিত করেছে নিজস্ব রূপে।
সাহিত্য শুধু বিনোদন নয়, তা মানুষকে ভাবায়, সচেতন করে, প্রতিবাদ করতে শেখায়। সাহিত্যের শক্তিতেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধিকার সংগ্রামের চেতনা জেগে উঠেছে।
এই প্রবাদ আমাদের শিক্ষা দেয়—সাহিত্যকে অবহেলা নয়, বরং জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে দেখতে হবে। কেননা সাহিত্য ছাড়া জাতি হয় বর্ণহীন, ইতিহাসহীন।
রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।
এই গভীরতাসম্পন্ন প্রবাদটি আশার আলোয় ভরসা রাখার এক চিরন্তন বার্তা বহন করে। মানুষ যখন গভীর দুঃখে, অন্ধকারে ডুবে যায়, তখন এই কথাটি তাকে সাহস দেয়—অন্ধকার যত গভীর, আলো ততই আসন্ন।
জীবনের প্রতিটি সংকট, হতাশা, ক্লান্তি—সবই একেকটি রাত। কিন্তু এই রাত চিরস্থায়ী নয়। যেমন প্রকৃতিতে রাতের পর আসে প্রভাত, তেমনি জীবনের প্রতিকূলতার পর আসে শান্তি, সাফল্য ও আলো।
এই প্রবাদটি আমাদের শেখায়—নিরাশ হওয়া নয়, বরং প্রতীক্ষা করতে জানতে হবে। কারণ দুঃখ যত গভীর, ততই তা আনন্দের সম্ভাবনা তৈরি করে। যেমন স্বাধীনতা এসেছে দীর্ঘ সংগ্রামের পর, সফলতা এসেছে ব্যর্থতার পর, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এসেছে যন্ত্রণা থেকে।
পৃথিবীর ইতিহাসে মহৎ অর্জনের পেছনে ছিল অনিদ্র রাত, ক্লান্তির অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্গবন্ধু—তাঁদের জীবনের ‘রাত’ দীর্ঘ হলেও তাঁরা হাল ছাড়েননি। ফলে এসেছে আলোর প্রভাত।
এই প্রবাদ আমাদের আশাবাদী করে তোলে। কঠিন সময় পেরিয়ে যদি আমরা ধৈর্য ধরি ও নিজেকে প্রস্তুত করি, তবে সকাল আসবেই। মনে রাখতে হবে—অন্ধকারে না হারালে আলো চেনা যায় না।
গতি যার নিচ সহ, নিচ সে দুর্মতি
এই প্রবাদটি অত্যন্ত তাৎপর্যময় এবং চারিত্রিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। যার মনোভাব নিচ, দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ও হীন, তার অগ্রগতিও হয় নিচগামী, নীতিবর্জিত ও ক্ষতিকর। সমাজে অনেক সময় আমরা দেখি কেউ হয়তো আর্থিক বা সামাজিকভাবে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু তার চিন্তা, আচরণ ও উদ্দেশ্য থাকে দুর্বৃত্তের মতো।
প্রকৃত উন্নতি কেবল বাহ্যিক নয়—আত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক হতে হয়। একজন দুর্মতি ব্যক্তি নিজের স্বার্থে অন্যকে ঠকায়, সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়, এবং গতি অর্জন করলেও সে সমাজের জন্য হয় বিপজ্জনক।
এই প্রবচনটি আমাদের সতর্ক করে দেয়—গতি মানেই উন্নতি নয়। গতি যদি অপথে হয়, তবে তা ব্যক্তিকে যেমন ধ্বংস করে, তেমনি সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।
যেমন—দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, অসৎ ব্যবসায়ী, কিংবা শোষক ধনীরা হয়তো গতি অর্জন করেছে, কিন্তু তাদের চরিত্র নিচ বলে সেই গতি হয়ে দাঁড়ায় সমাজের জন্য অভিশাপ।
সত্যিকারের উন্নতি হলো—যেখানে চরিত্র, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের সমন্বয় থাকে। তাই এই প্রবাদ আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়—গতি অর্জনের আগে চরিত্র গঠনের প্রয়োজন।
মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।
এই প্রবাদটি মানবজীবনের প্রকৃত ধনের অর্থকে ব্যাখ্যা করে। আমাদের সমাজে অনেকেই অর্থ, বিলাস ও বাহ্যিক প্রদর্শনকেই ‘ধন’ মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যার মধ্যে অপরের উপকার করার ক্ষমতা আছে, সেই ব্যক্তিই ধনী।
ধন যদি কেবল নিজস্ব ভোগের জন্য হয়, তবে তা বিলাস মাত্র; কিন্তু যদি সেই ধন দিয়ে গরিবের দুঃখ দূর করা যায়, শিক্ষা বিস্তার হয়, সমাজে শান্তি আসে—তবে সেটাই প্রকৃত ধন। মানুষের আসল পরিচয় তার দানশীলতায়, তার ব্যবহারযোগ্যতায়।
একজন ব্যক্তি কত গাড়ি চড়লেন, কত পোশাক বদলালেন, তা নয়; বরং তিনি কতজনকে হাসি দিলেন, কতজনের দুঃখে পাশে দাঁড়ালেন—তাই তাকে মহৎ করে তোলে।
আমাদের ইতিহাসে অনেক দানবীর ও সমাজসেবক আছেন যাঁরা অর্থ, জ্ঞান বা শ্রম দিয়ে সমাজের মঙ্গল করেছেন। যেমন বিদ্যাসাগর, রোকেয়া সাখাওয়াত, বা বঙ্গবন্ধু—তাঁদের ধন ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত।
এই প্রবাদটি আমাদের শিখিয়ে দেয়—ব্যক্তিগত বিলাস নয়, মানবকল্যাণে ব্যবহৃত সম্পদই সত্যিকারের ধন। কারণ তা-ই মানুষকে স্মরণীয় করে তোলে।
মিথ্যা শুনিনি ভাই, এ হৃদয়ের চেয়ে বর কোন মন্দির কাবা নাই।
এই পঙ্ক্তিটির গভীরে রয়েছে হৃদয়ের মহত্ত্বের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপাসনালয়ও যে মানুষের হৃদয়ের মতো পবিত্র নয়, এ বক্তব্য তারই প্রতিফলন।
হৃদয় হলো সহানুভূতির, ভালোবাসার, ক্ষমার আর মানবতার কেন্দ্র। এখানে ধর্ম, জাত, গাত্রবর্ণ বা অবস্থার প্রাচীর নেই—যেখানে সত্য, শান্তি ও সৌন্দর্যের বাস। এক নিষ্কলুষ হৃদয়ই পারে মানুষের দুঃখ বুঝতে, ভালোবাসতে এবং অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে।
পৃথিবীর সব ধর্ম হৃদয়ের পরিশুদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়। কাবা, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা—সবই বাহ্যিক প্রতীক; কিন্তু হৃদয় যদি কলুষিত হয়, তবে হাজারবার প্রার্থনাতেও সে পবিত্র হয় না। তাই কবি বলেছেন—হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো উপাসনালয় নেই।
এমন হৃদয় যে গরিবের কান্না বোঝে, সত্যের জন্য কাঁদে, এবং অসহায়ের পাশে দাঁড়ায়—সেই হৃদয়ই প্রকৃত পবিত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নজরুলের বিদ্রোহ, কিংবা সুফিদের বাণী—সবই হৃদয়ের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মেনেছে।
এই প্রবাদ আমাদের আত্মশুদ্ধির কথা বলে। বাহ্যিক আচারে নয়, হৃদয়ের জাগরণেই নিহিত আছে ঈশ্বরচেতনা।
অতৃপ্তিই অসুখের মূল।
এই প্রবাদটি মানব জীবনের চিরন্তন সত্যকে স্পষ্ট করে—লোভ, অতৃপ্তি এবং চাহিদার অস্থিরতা থেকেই জীবনের অধিকাংশ অসুখের জন্ম হয়।
যে মানুষ কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে সর্বদা অস্থির, অশান্ত এবং বিষণ্ন থাকে। অথচ জীবনের প্রকৃত সুখ লুকিয়ে থাকে মনের শান্তি ও সহজ সরলতায়। অতৃপ্তি মানুষকে করে লোভী, ঈর্ষান্বিত এবং আত্মকেন্দ্রিক।
যার একজোড়া জুতো আছে, সে চায় দশজোড়া; যার কুঁড়েঘর আছে, সে চায় প্রাসাদ। এই চাহিদা চিরকালীন, এবং তৃপ্তির অভাবে তা রূপ নেয় অসুখে।
বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরাও বলেছেন—মানুষের আসল সুখ বাহ্যিক সম্পদে নয়, অন্তরের শান্তিতে। অতৃপ্ত মন চায় আরও, আর তাতেই জন্ম নেয় হিংসা, যুদ্ধ, ও সংঘাত।
এই প্রবাদটি আমাদের আত্মসমালোচনা করতে শেখায়—আমরা কী চাইছি, কেন চাইছি এবং তার জন্য কী হারাচ্ছি? অপ্রয়োজনীয় চাহিদা সীমিত করলেই মানসিক শান্তি ও জীবনের ভারসাম্য ফিরে আসে।
তাই সত্যিকার সুখের প্রথম শর্ত হলো—তৃপ্তি শেখা। অতৃপ্তি নয়, আত্মতুষ্টিই মানুষকে করে আনন্দিত।
বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
এই প্রবাদটি স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক অবস্থানের সঠিকতার এক চমৎকার রূপক উপস্থাপন করে। প্রত্যেক প্রাণী, ব্যক্তি বা জিনিস তার নিজস্ব পরিবেশেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও সুন্দর।
বন্য পশু বনেই তার স্বাধীনতা ও সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজ করে। তাকে খাঁচায় আটকে রাখলে সে হয়ে যায় বিষণ্ন ও নিষ্প্রভ। তেমনি শিশু মাতৃক্রোড়েই পায় শান্তি, স্নেহ ও নিরাপত্তা। এই স্বাভাবিক অবস্থানই জীবনের সত্য সৌন্দর্য।
এই প্রবচনটি আমাদের শেখায়—প্রকৃতিকে তার নিজের ছন্দে চলতে দিতে হবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করলে তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম, কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর।
এছাড়াও, প্রবচনটি সামাজিক-মানবিক গুরুত্ব বহন করে। শিশুরা যেন তাদের মা ও পরিবারের আশ্রয়ে বড় হতে পারে, সেটাই সমাজের অন্যতম দায়িত্ব। শিশুকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করে রাখলে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
তাই এই প্রবচন কেবল প্রকৃতির রূপক নয়, এটি এক মানবিক আহ্বানও—স্বাভাবিকতা বজায় রাখার, নিজের আপন জায়গাকে শ্রদ্ধা করার, এবং সঠিক পরিবেশে বিকাশের সুযোগ দেওয়ার।
মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।
এই প্রবাদটি জীবনের সার্থকতা ও মানে বোঝাতে চমৎকার এক দিক নির্দেশ করে। একজন মানুষের সত্য পরিচয় তার বয়সে নয়, বরং তার কর্মে। কেউ হয়তো অল্প বয়সে পৃথিবীকে বদলে দেয়, আবার কেউ দীর্ঘজীবী হয়েও কিছু রেখে যেতে পারে না।
জীবনকে বড় করে তোলে শুধু কর্ম—সৃজনশীল, মানবিক ও কল্যাণময় কাজ। তাই আমাদের বলা হয়, কীর্তির মাধ্যমে অমর হও—জীবন দীর্ঘ নয়, মহৎ হোক।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতির জনক—তাঁর জীবন বেশি দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু তাঁর কর্ম আজও অনুপ্রেরণা। তেমনি নজরুল, সত্যেন বসু, কিংবা বেগম রোকেয়া—তাঁদের প্রতিটি কর্ম জীবনকে দিয়েছে মহত্ব।
এই প্রবাদ আমাদের শেখায়—সময় নয়, বরং কীভাবে সময়কে ব্যবহার করছ তা জরুরি। বয়স বড় হওয়া মানেই মানুষ হওয়া নয়; বরং কর্মে, দায়িত্বে, ত্যাগে এবং অবদানে মানুষ নিজেকে বড় করে তোলে।
জীবনকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও নিষ্ঠা। এই প্রবাদ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচতে, যেন মৃত্যুর পরও আমরা কর্মের মধ্যে জীবিত থাকি।
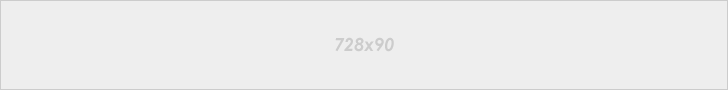

No comments